
রাসেল রায়হান

বই আলোচনা‘
প্রথম দৃশ্যটির নাম—আলোর উঠোন
দৃশ্যটির চূড়ায় বসে লেজ নাড়ে বাঘ
বিভিন্ন ধাপে—পাদদেশে
নেকড়ে হায়েনা শেয়াল...
অন্য দৃশ্যটির নাম—অন্ধকারের খোঁয়াড়
দৃশ্যটির চূড়ায় বসে জাবর কাটে গরু
বিভিন্ন ধাপে—পাদদেশে
ভেড়া ছাগল মহিষ...
দুটি দৃশ্যের মাঝখানে ঘ্রাণছোঁয়া ফাঁক
সেখানে ছোপ ছোপ দাগ...’
[‘কার্টুনছবির কবিতা’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ১১৫]
এক যুবকের উদাহরণ টানা যায়, যার প্রেমিকা সদ্য তাকে পরিত্যাগ করে প্রবাসী এক যুবককে বিয়ে করে বিদেশে চলে গিয়েছে। যুবকটি তার প্রেমিকার ওপর রেগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাড়ির পছন্দে যাকে খুশি বিয়ে করবে। এমনকি পাত্রীর ছবিও সে দেখেনি। বিয়ের পর ফুলশয্যায় গিয়েই তার চোখ পড়ে নতুন বউয়ের আড়ষ্ট হাতে। দেখেই চমকে যায় সে। এই হাত তার পরিচিত। অজস্রবার এই হাতের আঙুল সে ধরেছে প্রেমে-অপ্রেমে। তার মনে কামড় দিল, আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে তার প্রেমিকা আসলে কোনো প্রবাসীকে বিয়ে করেনি? বাবা-মা যে পাত্রীকে তার জন্য ঠিক করেছেন, সে আসলে তার সেই প্রেমিকা! হয়তো। আবার হয়তো না। হয়তো বাবা-মা পুত্রের প্রেমের কথা জেনেশুনে নিজেরাই এই উদ্যোগ নিয়েছেন। তার প্রেমিকাটি এটা লুকিয়েছে সযত্নে। অসম্ভব না। প্রেমিকাটির রহস্য করা স্বভাব সম্পর্কে তো সে আগে থেকেই জানে। যুবক কাঁপা কাঁপা হাতে ঘোমটার দিকে হাত বাড়ায়। আসলেই কি সে?
ঘোমটা সরিয়ে চমকে যায় যুবক। আসলেই তো সেই প্রেমিকা! কড়া মেকআপ মেখেছে বলে সামান্য অন্য রকম লাগছে অবশ্য। সামান্যই? নাকি অনেক বেশি অন্যরকম? আসলেই কি প্রেমিকাটি? নাকি অন্য কোনো নারী, যার চেহারার সঙ্গে প্রেমিকাটির স্পষ্ট মিল? যুবক বিভ্রান্ত হয়ে যায়। স্পর্শ করবে কী করবে না—ভাবতে থাকে...।
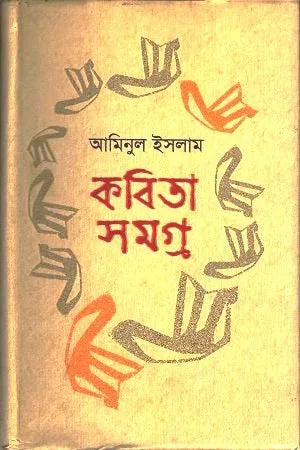
সম্ভবত কবিতা হলো ঘোমটা পরা সেই বউ, যাকে দেখে পাঠক বিভ্রান্ত হবে। সঠিকের কাছাকাছি যাবে, কিন্তু একদম সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবে না। অনেকটা শহীদ কাদরীর ‘কোথাও শান্তি পাবে না পাবে না পাবে না’র পরিস্থিতি।
বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন কবিতার সংজ্ঞা। মজার ব্যাপার হলো, এই সংজ্ঞা সবাই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী দিতে পারেননি, দেওয়া যায়ও না, যতটা সহজে নিজের রুচি অনুযায়ী লেখা যায় কবিতা; পাঠও করা যায়। যেখানে কবিতা কী—এরই একক কোনো সংজ্ঞা এখনো আমার জানা নেই, সেখানে আধুনিক কবিতা কী—এই তর্ক ওঠাতে সাহস না পাওয়াই স্বাভাবিক আমার কাছে।
আমিনুল ইসলামের ‘কবিতা সমগ্র’ পাঠে একটি সিদ্ধান্তে অবশ্য সহজেই আসা যায়। তার কবিতা প্রায় সকল সংজ্ঞাই ধারণ করেছে। কোথাও পর্যাপ্ত আড়াল, কোথাও পর্যাপ্ত উন্মোচন, কোথাও নমনীয়ভাবে আওড়ানো ছন্দের নরম নদী, কোথাও মানবিকতার স্বার্থে উচ্চারিত উঁচু আওয়াজে দূরের বৃক্ষ থেকে উড়ে যায় পাখি, ডুব দেয় অক্সিজেন নিতে উপরিভাগে উঠে আসা মাছ, পানিতে নেমে যায় রোদ পোহাতে থাকা কুমির। এক কথায় বলতে গেলে আমিনুল ইসলামের কবিতা ধারণ করে সময়কে এবং সেগুলি কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রেখে, শিল্পের স্বার্থে সামান্যও ছাড় না দিয়ে।
‘প্রাপ্তবয়স্ক প্রেমিকের সাজ পরে তার কাছে যাই
আর ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি:
উদার স্তনের নিচে মুখ দিয়ে শুয়ে আছি আমি দুধের শিশু।’
[‘সে এক অদ্ভুত ব্যর্থতা’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ১৩৩]
আমিনুল ইসলামের কবিতা মূলত সমকালে বসে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের কবিতা। সে কবিতা মানুষকে তার নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রেম, বেদনা, যন্ত্রণা, ক্ষুধা, রাজনীতি, শরীর, অশরীর এতটা পরিমিতভাবে এসেছে যে মাঝে মাঝে অবাক হতে হয়। সব মিলিয়ে মানুষের জীবন এসেছে স্পষ্টভাবে। সে জীবন আয়নার বিভ্রান্তিময় বিম্ব নয় যে ডান হাতকে বাঁ হাত আর বাঁ হাতকে ডান হাত মনে হবে। সে জীবন আমাদের চোখে দেখা জীবন। সেখানে ডান হাতকে ডান হাতই মনে হয়, আর বাঁ হাতকে স্পষ্টতই বাঁ হাত।
কবিতা সমগ্রের শুরুতে ভূমিকা পড়লেই আমিনুল ইসলামের কবিতার ভিত টের পাওয়া যায় অনেকটা স্পষ্টভাবে। প্রকৃতি তাঁকে শৈশব থেকেই ডেকেছে, নিয়তিক্রমে চাকরি সূত্রে সেই ডাকের জবাবও দিয়েছেন তিনি। ঘুরেছেন বিভিন্ন জায়গায়। আর তার প্রভাব পড়েছে তাঁর কবিতায় যত্রতত্র, উদারভাবে। সোনা মসজিদ, মহাস্থানগড়, উয়ারী বটেশ্বর, পাহাড়পুর বিহার, বেহুলার ভিটাসহ মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া, তুরস্ক—এমন অজস্র ঐতিহাসিক জায়গার ঘ্রাণ ভেসে বেড়ায় তার কবিতায়। সেসব কবিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবুজের। রঙ ছড়ায় সবুজ। পিতার ফেলে রাখা সবুজ পাণ্ডুলিপি হয়ে হাহাকার করে। অনূদিত হয় আমিনুল ইসলামের কলমে।
‘বৃক্ষ-নদী-ফসলের মাঠ-ভোরের হাওয়া—
সবার সাথে আড্ডা ছিল বাবার
আমি তো বহু ধরনের বর্ণমালা চিনি
কিন্তু বাবার রেখে-যাওয়া কবিতার মানে বুঝি না।
অনুবাদ করব বলে টেবিলে বসি—
কিন্তু কীভাবে করব সে অনুবাদ?’
[‘আমার পিতার কবিতার অনুবাদ’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ১১১]

আমিনুল ইসলাম নিজের সীমাবদ্ধতা জেনেও প্রকৃতিকে অনুবাদ করার চেষ্টা করেন। ‘বৃক্ষের জন্য শোকগাঁথা’ রচনা করেন বাঁশিহাতে। বনসাইয়ের প্ররোচিত জীবন ছেড়ে তিনি চোখের সামনে তুলে ধরেন মহিমাময় মহীরুহের আবেদন। শরত এবং হেমন্তের সে সংবাদ আমরা পাঠ হতে শুনি আমিনুল ইসলামের কণ্ঠে, সে সংবাদও প্রকৃতি থেকে নিংড়ে আনা, নিংড়ে আনা ইতিহাস থেকে। হ্যাঁ, ইতিহাস বারবার ঘুরেফিরে আসে আমিনুল ইসলামের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জীবনানন্দ দাশ—ইতিহাস আরও অনেক কবির কবিতাতেই এসেছে। কিন্তু আমিনুল ইসলাম ইতিহাসের ব্যবহার করেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে। ‘মাফ করে দাও বাবা/“পূর্ব পাকিস্তান” শব্দটির মতো বাতিল হয়ে গেছে/তোমার শেখানো সে তরিকা’ এর একটি সাধারণ উদাহরণই হতে পারে।
এই সেই সোনা মসজিদ—আমাদের পূর্বজনদের প্রেম ও ঘামের সাক্ষী;
ঘূণে-পোকার ঈর্ষা জাগিয়ে তাকে কাটে দিনরাত—কালের করাত আর
ছদ্মবেশী ইঁদুর; স্রোতখোয়া নদীপাড়ের মতো কখন যে ভেঙে পড়ে!
দ্যাখো, এইখানে স্বর্গীয় ছায়ায় শুয়ে একাত্তরের তিতুমীর—যাকে ভালো
বেসে বরণ করে নিতে আন্ধাসা...
...এই যে পথে পথে বাগানের
ছায়া—এই ছায়ায় বসে জিরিয়েছিলেন তুর্কী সেনাপতি আর তার ঘর্মাক্ত ঘোড়াটি;
...দ্যাখো—মন্দিরের পায়ের নিচে পায়ের
পাতার মতো সমতলভূমি; এখানেই ছিল সেই নদী আর সেই
গন্ধেশ্বরীর ঘাট; আহাঁটু উদোম পা ছড়িয়ে সন্ধ্যাবতী কতদিন
বসেছেন এই ঘাটে!...
...এই যে আজকের সুরম্য শহর—একদিন এখানেই
গড়ে উঠেছিল সভ্যতার মাতৃঘর পুণ্ড্রনগর—
[‘পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ২৪৪, ২৪৫ ও ২৪৬]
একটিমাত্র দীর্ঘকবিতার সামান্য অংশ এটি। সম্পূর্ণ কবিতাটি উল্লেখ করার লোভ সামলালাম। পাঠান্তরে অনুভব করবেন, কী করে একটি কবিতা আপনাকে টেনে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারে ইতিহাস ও মিথের আদি বাংলায়, মুহূর্তেই আবার নিয়ে আসে এখানে, বর্তমানে, এই যুগে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কবিতায় মিথের সহজ ও সক্ষম ব্যবহার। মিথের ব্যবহার এতটা সাবলীল আর বিশ্বাসযোগ্যভাবে করেছেন আমিনুল ইসলাম, যে এক মুহূর্তের জন্য মিথকে আর মিথ মনে হবে না, মনে হবে জ্বলজ্যান্ত ইতিহাস। মনে হবে সেই ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলে যাচ্ছেন কবি। মনে হবে কোনো প্রাচীন শিক্ষক খুলে দিচ্ছেন তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার স্বর্গীয় ভান্ডার। সে বর্ণনা সিনেমার পর্দার মতো, ধারাবাহিক ঢেউয়ের মতো। ঢেউয়ের মতোই আদি বাংলার কথা বলতে বলতে আমিনুল ইসলাম আপনাকে নিয়ে যাবেন পরিচিত দেশের বাইরে, অন্য অভিজ্ঞতায়, সেখান থেকে আবার এই বাংলায়।
আঙ্কারা থেকে সানলিউর্ফা বা হারানো দিনের উর্ফা; অতঃপর ইস্তাম্বুল
উর্ফা শহরে আইয়ুব নবীর প্রেম ও ধ্যানের গুহা; কালের সাক্ষী আইয়ুব মসজিদও।
...তোমার ঠোঁটের মতে পবিত্র নবীর ইন্দারা।
...বসফরাসের খোলা হাওয়ায় খোলেনি সে এতটুকু! তার
মনজুড়ে করতোয়া আর আঁচলে সুন্দরবন।
[‘ইস্তাম্বুলের ই-মেইল’, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২১৬, ২১৭]
আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা আছে, তর্ক আছে বহু আগে থেকেই। এসব নিয়ে আমারও সামান্য কিছু ভাবনা আছে, বাধ্য হয়েই পুরনো জের টানছি। যেখানে আধুনিকতা নিয়েই এত তর্ক, সেখানে এখন পৌঁছে গেছি আধুনিকের যুগ পার করে উত্তরাধুনিকের কালে; সেটাও পার করে ফেলেছি আমরা, অনেকের দাবিমতে। কাল থেকে কালান্তরে এই যাত্রা স্বতঃস্ফূর্ত, সেটা যে নাম দিয়েই বিশেষায়িত করা হোক না কেন। আমার কাছে অবশ্য আধুনিক শব্দটিকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং আধুনিক মনে হয়। যখন আধুনিক পুরনো হয়ে যায়, সেখানে নতুন করে আসে আরেক আধুনিক, আবার সেটিকে অস্বীকার কিংবা স্বীকার করে সৃষ্টি হয় অন্য আরেক আধুনিকের। পূর্বের আধুনিকগুলো ক্রমশ পুরাতন হয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে কেউ কেউ সময়কে অতিক্রম করতে পারেন। যারা পারেন তারাই টিকে যান, যতটুকু সময়কে ছুঁতে পারেন, ততটুকু সময় পর্যন্ত। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইদানীং, যেমন: আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য, পরাবাস্তবতার ওপরে ভর করে তা পাঠক থেকে সহস্র মাইল দূরে সরে যাচ্ছে। এইসব অভিযোগ মাথায় নিয়ে কবিরা লিখে যাচ্ছেন আধুনিক কবিতা। পাঠক নিজে যথেষ্ট প্রস্তুত হচ্ছে না, অথচ কবিরাও তাদের কাছে যাওয়াকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছে না, আবার হালকা স্বরে লিখতেও পারছে না—এমন কিছু দ্বিধাময়তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলা কবিতা।
এই দ্বিধাসঙ্কুল পরিবেশেই কবিদের মধ্যে ভর করছে আরও পরাবাস্তবতা, আরও দুর্বোধ্যতা। রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের দোহাই দিয়ে সত্যিকার অর্থে কষ্টকল্পিত কিছু জিনিসেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বাংলা কবিতা। আর পাঠকও একধরনের প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছেন এই কবিতা সম্পর্কে। অনেকটা ব্যাটসম্যান যেমন আগে থেকেই অনেক সময় প্রস্তুত হয়ে থাকেন বড় শট হাঁকানোর, কিংবা আগেই ডিফেন্স করার। ক্রিকেটবোদ্ধা মাত্রই জানেন, আগাম এ ধরনের প্রস্তুতির ফল কখনোই ভালো হয় না। কবিতাতেও বর্তমান পাঠক এ ধরনের কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। ফলে সত্যিকারের ভালো বলে মারতে গিয়ে তারা অহরহ বোল্ড হয়ে যাচ্ছে, কিংবা কট বিহাইন্ড হয়ে ফিরে যাচ্ছে (পড়ুন ভালো কবিতা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে পুরনো ডেরায়)। সত্যিকারের উপমা তারা বুঝতে পারছেন না, রূপক ধরতে পারছেন না। ইঙ্গিতকে ভাবছেন বোবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এবার আসি আমিনুল ইসলামে।
ঘোড়ার কাহিনি থাক্
এ নহে প্রস্তর যুগ
বৃষগুলো নেই
তবু গাভিগুলি গর্ভবতী
বারুদ প্রহরে
সমুদ্রের দুইপাড়ে
খচ্চরের শিশুগুলি দুধ খায়
কুমারী ওরানে;...
ওগো মাতা বসুমতী
তোমার গোয়াল ভরে
কত কাজ হলো—
[‘গোত্রশুমারি’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ১১৬]
আমিনুল ইসলাম কবিতা বলেন সহজভাবে। চিত্রকল্প থাকে, সমস্ত অলংকার থাকে, কিন্তু সেসবের বাহুল্য কমই পাওয়া যায় তার কবিতায়। কবিতায় অমোঘ বলতে যেমন কিছু নেই, তেমনি কিছু অলংকার ব্যতীত কবিতাকে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এই অলংকারকে আমিনুল ইসলাম কবিতায় ব্যবহার করেন পাকা আলংকারিকের ঢঙে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো সেসব অলংকার বানানো বা চাপিয়ে দেওয়া নয়। ঝরঝরে ও সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি। পরিমিতিবোধের এক আশ্চর্য পরিবেশ সেখানে। কোনো দুর্বোধ্যতা নেই। আছে রূপক, ইঙ্গিত। আমাদের নিজেদের গল্পই শোনা যায় এখানে। তাঁর কবিতায় প্রেম আছে, সেখানে এক ধরনের অস্থিরতা এবং কোমলতার মিশেলও আছে। আছে আঁটসাঁট রহস্যময়তা ও ইঙ্গিতময়তা। কবিতাকে তখন ভারবাহী খচ্চর মনে না হয়ে সজ্জিত গৃহবধূই মনে হয়। আমিনুল ইসলাম সেই গৃহবধূ কবিতার ‘স্বামী’ নয়, মনিব। এবং প্রেমিকও।
রাসেল রায়হান: কবি ও কথাশিল্পী, ঢাকা।
**প্রিয় পাঠক, বিডিজেন২৪-এ গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি, সুখ–দুঃখের স্মৃতি, প্রবন্ধ, ফিচার, অনুষ্ঠান বা ঘটনার ভিডিও এবং ছবিসহ নানা বিষয়ের লেখা পাঠান। মেইল: [email protected]

বই আলোচনা‘
প্রথম দৃশ্যটির নাম—আলোর উঠোন
দৃশ্যটির চূড়ায় বসে লেজ নাড়ে বাঘ
বিভিন্ন ধাপে—পাদদেশে
নেকড়ে হায়েনা শেয়াল...
অন্য দৃশ্যটির নাম—অন্ধকারের খোঁয়াড়
দৃশ্যটির চূড়ায় বসে জাবর কাটে গরু
বিভিন্ন ধাপে—পাদদেশে
ভেড়া ছাগল মহিষ...
দুটি দৃশ্যের মাঝখানে ঘ্রাণছোঁয়া ফাঁক
সেখানে ছোপ ছোপ দাগ...’
[‘কার্টুনছবির কবিতা’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ১১৫]
এক যুবকের উদাহরণ টানা যায়, যার প্রেমিকা সদ্য তাকে পরিত্যাগ করে প্রবাসী এক যুবককে বিয়ে করে বিদেশে চলে গিয়েছে। যুবকটি তার প্রেমিকার ওপর রেগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাড়ির পছন্দে যাকে খুশি বিয়ে করবে। এমনকি পাত্রীর ছবিও সে দেখেনি। বিয়ের পর ফুলশয্যায় গিয়েই তার চোখ পড়ে নতুন বউয়ের আড়ষ্ট হাতে। দেখেই চমকে যায় সে। এই হাত তার পরিচিত। অজস্রবার এই হাতের আঙুল সে ধরেছে প্রেমে-অপ্রেমে। তার মনে কামড় দিল, আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে তার প্রেমিকা আসলে কোনো প্রবাসীকে বিয়ে করেনি? বাবা-মা যে পাত্রীকে তার জন্য ঠিক করেছেন, সে আসলে তার সেই প্রেমিকা! হয়তো। আবার হয়তো না। হয়তো বাবা-মা পুত্রের প্রেমের কথা জেনেশুনে নিজেরাই এই উদ্যোগ নিয়েছেন। তার প্রেমিকাটি এটা লুকিয়েছে সযত্নে। অসম্ভব না। প্রেমিকাটির রহস্য করা স্বভাব সম্পর্কে তো সে আগে থেকেই জানে। যুবক কাঁপা কাঁপা হাতে ঘোমটার দিকে হাত বাড়ায়। আসলেই কি সে?
ঘোমটা সরিয়ে চমকে যায় যুবক। আসলেই তো সেই প্রেমিকা! কড়া মেকআপ মেখেছে বলে সামান্য অন্য রকম লাগছে অবশ্য। সামান্যই? নাকি অনেক বেশি অন্যরকম? আসলেই কি প্রেমিকাটি? নাকি অন্য কোনো নারী, যার চেহারার সঙ্গে প্রেমিকাটির স্পষ্ট মিল? যুবক বিভ্রান্ত হয়ে যায়। স্পর্শ করবে কী করবে না—ভাবতে থাকে...।
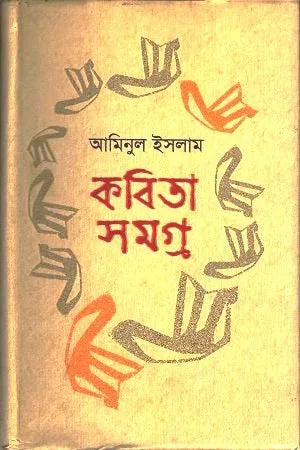
সম্ভবত কবিতা হলো ঘোমটা পরা সেই বউ, যাকে দেখে পাঠক বিভ্রান্ত হবে। সঠিকের কাছাকাছি যাবে, কিন্তু একদম সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারবে না। অনেকটা শহীদ কাদরীর ‘কোথাও শান্তি পাবে না পাবে না পাবে না’র পরিস্থিতি।
বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে দিয়েছেন কবিতার সংজ্ঞা। মজার ব্যাপার হলো, এই সংজ্ঞা সবাই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী দিতে পারেননি, দেওয়া যায়ও না, যতটা সহজে নিজের রুচি অনুযায়ী লেখা যায় কবিতা; পাঠও করা যায়। যেখানে কবিতা কী—এরই একক কোনো সংজ্ঞা এখনো আমার জানা নেই, সেখানে আধুনিক কবিতা কী—এই তর্ক ওঠাতে সাহস না পাওয়াই স্বাভাবিক আমার কাছে।
আমিনুল ইসলামের ‘কবিতা সমগ্র’ পাঠে একটি সিদ্ধান্তে অবশ্য সহজেই আসা যায়। তার কবিতা প্রায় সকল সংজ্ঞাই ধারণ করেছে। কোথাও পর্যাপ্ত আড়াল, কোথাও পর্যাপ্ত উন্মোচন, কোথাও নমনীয়ভাবে আওড়ানো ছন্দের নরম নদী, কোথাও মানবিকতার স্বার্থে উচ্চারিত উঁচু আওয়াজে দূরের বৃক্ষ থেকে উড়ে যায় পাখি, ডুব দেয় অক্সিজেন নিতে উপরিভাগে উঠে আসা মাছ, পানিতে নেমে যায় রোদ পোহাতে থাকা কুমির। এক কথায় বলতে গেলে আমিনুল ইসলামের কবিতা ধারণ করে সময়কে এবং সেগুলি কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রেখে, শিল্পের স্বার্থে সামান্যও ছাড় না দিয়ে।
‘প্রাপ্তবয়স্ক প্রেমিকের সাজ পরে তার কাছে যাই
আর ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখি:
উদার স্তনের নিচে মুখ দিয়ে শুয়ে আছি আমি দুধের শিশু।’
[‘সে এক অদ্ভুত ব্যর্থতা’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ১৩৩]
আমিনুল ইসলামের কবিতা মূলত সমকালে বসে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের কবিতা। সে কবিতা মানুষকে তার নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রেম, বেদনা, যন্ত্রণা, ক্ষুধা, রাজনীতি, শরীর, অশরীর এতটা পরিমিতভাবে এসেছে যে মাঝে মাঝে অবাক হতে হয়। সব মিলিয়ে মানুষের জীবন এসেছে স্পষ্টভাবে। সে জীবন আয়নার বিভ্রান্তিময় বিম্ব নয় যে ডান হাতকে বাঁ হাত আর বাঁ হাতকে ডান হাত মনে হবে। সে জীবন আমাদের চোখে দেখা জীবন। সেখানে ডান হাতকে ডান হাতই মনে হয়, আর বাঁ হাতকে স্পষ্টতই বাঁ হাত।
কবিতা সমগ্রের শুরুতে ভূমিকা পড়লেই আমিনুল ইসলামের কবিতার ভিত টের পাওয়া যায় অনেকটা স্পষ্টভাবে। প্রকৃতি তাঁকে শৈশব থেকেই ডেকেছে, নিয়তিক্রমে চাকরি সূত্রে সেই ডাকের জবাবও দিয়েছেন তিনি। ঘুরেছেন বিভিন্ন জায়গায়। আর তার প্রভাব পড়েছে তাঁর কবিতায় যত্রতত্র, উদারভাবে। সোনা মসজিদ, মহাস্থানগড়, উয়ারী বটেশ্বর, পাহাড়পুর বিহার, বেহুলার ভিটাসহ মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া, তুরস্ক—এমন অজস্র ঐতিহাসিক জায়গার ঘ্রাণ ভেসে বেড়ায় তার কবিতায়। সেসব কবিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবুজের। রঙ ছড়ায় সবুজ। পিতার ফেলে রাখা সবুজ পাণ্ডুলিপি হয়ে হাহাকার করে। অনূদিত হয় আমিনুল ইসলামের কলমে।
‘বৃক্ষ-নদী-ফসলের মাঠ-ভোরের হাওয়া—
সবার সাথে আড্ডা ছিল বাবার
আমি তো বহু ধরনের বর্ণমালা চিনি
কিন্তু বাবার রেখে-যাওয়া কবিতার মানে বুঝি না।
অনুবাদ করব বলে টেবিলে বসি—
কিন্তু কীভাবে করব সে অনুবাদ?’
[‘আমার পিতার কবিতার অনুবাদ’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ১১১]

আমিনুল ইসলাম নিজের সীমাবদ্ধতা জেনেও প্রকৃতিকে অনুবাদ করার চেষ্টা করেন। ‘বৃক্ষের জন্য শোকগাঁথা’ রচনা করেন বাঁশিহাতে। বনসাইয়ের প্ররোচিত জীবন ছেড়ে তিনি চোখের সামনে তুলে ধরেন মহিমাময় মহীরুহের আবেদন। শরত এবং হেমন্তের সে সংবাদ আমরা পাঠ হতে শুনি আমিনুল ইসলামের কণ্ঠে, সে সংবাদও প্রকৃতি থেকে নিংড়ে আনা, নিংড়ে আনা ইতিহাস থেকে। হ্যাঁ, ইতিহাস বারবার ঘুরেফিরে আসে আমিনুল ইসলামের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জীবনানন্দ দাশ—ইতিহাস আরও অনেক কবির কবিতাতেই এসেছে। কিন্তু আমিনুল ইসলাম ইতিহাসের ব্যবহার করেন সম্পূর্ণ নতুনভাবে। ‘মাফ করে দাও বাবা/“পূর্ব পাকিস্তান” শব্দটির মতো বাতিল হয়ে গেছে/তোমার শেখানো সে তরিকা’ এর একটি সাধারণ উদাহরণই হতে পারে।
এই সেই সোনা মসজিদ—আমাদের পূর্বজনদের প্রেম ও ঘামের সাক্ষী;
ঘূণে-পোকার ঈর্ষা জাগিয়ে তাকে কাটে দিনরাত—কালের করাত আর
ছদ্মবেশী ইঁদুর; স্রোতখোয়া নদীপাড়ের মতো কখন যে ভেঙে পড়ে!
দ্যাখো, এইখানে স্বর্গীয় ছায়ায় শুয়ে একাত্তরের তিতুমীর—যাকে ভালো
বেসে বরণ করে নিতে আন্ধাসা...
...এই যে পথে পথে বাগানের
ছায়া—এই ছায়ায় বসে জিরিয়েছিলেন তুর্কী সেনাপতি আর তার ঘর্মাক্ত ঘোড়াটি;
...দ্যাখো—মন্দিরের পায়ের নিচে পায়ের
পাতার মতো সমতলভূমি; এখানেই ছিল সেই নদী আর সেই
গন্ধেশ্বরীর ঘাট; আহাঁটু উদোম পা ছড়িয়ে সন্ধ্যাবতী কতদিন
বসেছেন এই ঘাটে!...
...এই যে আজকের সুরম্য শহর—একদিন এখানেই
গড়ে উঠেছিল সভ্যতার মাতৃঘর পুণ্ড্রনগর—
[‘পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ২৪৪, ২৪৫ ও ২৪৬]
একটিমাত্র দীর্ঘকবিতার সামান্য অংশ এটি। সম্পূর্ণ কবিতাটি উল্লেখ করার লোভ সামলালাম। পাঠান্তরে অনুভব করবেন, কী করে একটি কবিতা আপনাকে টেনে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারে ইতিহাস ও মিথের আদি বাংলায়, মুহূর্তেই আবার নিয়ে আসে এখানে, বর্তমানে, এই যুগে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কবিতায় মিথের সহজ ও সক্ষম ব্যবহার। মিথের ব্যবহার এতটা সাবলীল আর বিশ্বাসযোগ্যভাবে করেছেন আমিনুল ইসলাম, যে এক মুহূর্তের জন্য মিথকে আর মিথ মনে হবে না, মনে হবে জ্বলজ্যান্ত ইতিহাস। মনে হবে সেই ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলে যাচ্ছেন কবি। মনে হবে কোনো প্রাচীন শিক্ষক খুলে দিচ্ছেন তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার স্বর্গীয় ভান্ডার। সে বর্ণনা সিনেমার পর্দার মতো, ধারাবাহিক ঢেউয়ের মতো। ঢেউয়ের মতোই আদি বাংলার কথা বলতে বলতে আমিনুল ইসলাম আপনাকে নিয়ে যাবেন পরিচিত দেশের বাইরে, অন্য অভিজ্ঞতায়, সেখান থেকে আবার এই বাংলায়।
আঙ্কারা থেকে সানলিউর্ফা বা হারানো দিনের উর্ফা; অতঃপর ইস্তাম্বুল
উর্ফা শহরে আইয়ুব নবীর প্রেম ও ধ্যানের গুহা; কালের সাক্ষী আইয়ুব মসজিদও।
...তোমার ঠোঁটের মতে পবিত্র নবীর ইন্দারা।
...বসফরাসের খোলা হাওয়ায় খোলেনি সে এতটুকু! তার
মনজুড়ে করতোয়া আর আঁচলে সুন্দরবন।
[‘ইস্তাম্বুলের ই-মেইল’, কবিতাসমগ্র, পৃ. ২১৬, ২১৭]
আধুনিক কবিতা নিয়ে আলোচনা আছে, তর্ক আছে বহু আগে থেকেই। এসব নিয়ে আমারও সামান্য কিছু ভাবনা আছে, বাধ্য হয়েই পুরনো জের টানছি। যেখানে আধুনিকতা নিয়েই এত তর্ক, সেখানে এখন পৌঁছে গেছি আধুনিকের যুগ পার করে উত্তরাধুনিকের কালে; সেটাও পার করে ফেলেছি আমরা, অনেকের দাবিমতে। কাল থেকে কালান্তরে এই যাত্রা স্বতঃস্ফূর্ত, সেটা যে নাম দিয়েই বিশেষায়িত করা হোক না কেন। আমার কাছে অবশ্য আধুনিক শব্দটিকেই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং আধুনিক মনে হয়। যখন আধুনিক পুরনো হয়ে যায়, সেখানে নতুন করে আসে আরেক আধুনিক, আবার সেটিকে অস্বীকার কিংবা স্বীকার করে সৃষ্টি হয় অন্য আরেক আধুনিকের। পূর্বের আধুনিকগুলো ক্রমশ পুরাতন হয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে কেউ কেউ সময়কে অতিক্রম করতে পারেন। যারা পারেন তারাই টিকে যান, যতটুকু সময়কে ছুঁতে পারেন, ততটুকু সময় পর্যন্ত। আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইদানীং, যেমন: আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য, পরাবাস্তবতার ওপরে ভর করে তা পাঠক থেকে সহস্র মাইল দূরে সরে যাচ্ছে। এইসব অভিযোগ মাথায় নিয়ে কবিরা লিখে যাচ্ছেন আধুনিক কবিতা। পাঠক নিজে যথেষ্ট প্রস্তুত হচ্ছে না, অথচ কবিরাও তাদের কাছে যাওয়াকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছে না, আবার হালকা স্বরে লিখতেও পারছে না—এমন কিছু দ্বিধাময়তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলা কবিতা।
এই দ্বিধাসঙ্কুল পরিবেশেই কবিদের মধ্যে ভর করছে আরও পরাবাস্তবতা, আরও দুর্বোধ্যতা। রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পের দোহাই দিয়ে সত্যিকার অর্থে কষ্টকল্পিত কিছু জিনিসেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বাংলা কবিতা। আর পাঠকও একধরনের প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছেন এই কবিতা সম্পর্কে। অনেকটা ব্যাটসম্যান যেমন আগে থেকেই অনেক সময় প্রস্তুত হয়ে থাকেন বড় শট হাঁকানোর, কিংবা আগেই ডিফেন্স করার। ক্রিকেটবোদ্ধা মাত্রই জানেন, আগাম এ ধরনের প্রস্তুতির ফল কখনোই ভালো হয় না। কবিতাতেও বর্তমান পাঠক এ ধরনের কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। ফলে সত্যিকারের ভালো বলে মারতে গিয়ে তারা অহরহ বোল্ড হয়ে যাচ্ছে, কিংবা কট বিহাইন্ড হয়ে ফিরে যাচ্ছে (পড়ুন ভালো কবিতা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে পুরনো ডেরায়)। সত্যিকারের উপমা তারা বুঝতে পারছেন না, রূপক ধরতে পারছেন না। ইঙ্গিতকে ভাবছেন বোবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এবার আসি আমিনুল ইসলামে।
ঘোড়ার কাহিনি থাক্
এ নহে প্রস্তর যুগ
বৃষগুলো নেই
তবু গাভিগুলি গর্ভবতী
বারুদ প্রহরে
সমুদ্রের দুইপাড়ে
খচ্চরের শিশুগুলি দুধ খায়
কুমারী ওরানে;...
ওগো মাতা বসুমতী
তোমার গোয়াল ভরে
কত কাজ হলো—
[‘গোত্রশুমারি’, কবিতাসমগ্র: পৃ. ১১৬]
আমিনুল ইসলাম কবিতা বলেন সহজভাবে। চিত্রকল্প থাকে, সমস্ত অলংকার থাকে, কিন্তু সেসবের বাহুল্য কমই পাওয়া যায় তার কবিতায়। কবিতায় অমোঘ বলতে যেমন কিছু নেই, তেমনি কিছু অলংকার ব্যতীত কবিতাকে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এই অলংকারকে আমিনুল ইসলাম কবিতায় ব্যবহার করেন পাকা আলংকারিকের ঢঙে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো সেসব অলংকার বানানো বা চাপিয়ে দেওয়া নয়। ঝরঝরে ও সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি। পরিমিতিবোধের এক আশ্চর্য পরিবেশ সেখানে। কোনো দুর্বোধ্যতা নেই। আছে রূপক, ইঙ্গিত। আমাদের নিজেদের গল্পই শোনা যায় এখানে। তাঁর কবিতায় প্রেম আছে, সেখানে এক ধরনের অস্থিরতা এবং কোমলতার মিশেলও আছে। আছে আঁটসাঁট রহস্যময়তা ও ইঙ্গিতময়তা। কবিতাকে তখন ভারবাহী খচ্চর মনে না হয়ে সজ্জিত গৃহবধূই মনে হয়। আমিনুল ইসলাম সেই গৃহবধূ কবিতার ‘স্বামী’ নয়, মনিব। এবং প্রেমিকও।
রাসেল রায়হান: কবি ও কথাশিল্পী, ঢাকা।
**প্রিয় পাঠক, বিডিজেন২৪-এ গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি, সুখ–দুঃখের স্মৃতি, প্রবন্ধ, ফিচার, অনুষ্ঠান বা ঘটনার ভিডিও এবং ছবিসহ নানা বিষয়ের লেখা পাঠান। মেইল: [email protected]
তিনি প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত নিরলস প্রচারণা চালিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো রাজনৈতিক নেতার সহধর্মিণীর এমন সক্রিয় ও দীর্ঘ সময় মাঠে থাকার নজির খুব কমই দেখা যায়। তিনি শুধু মঞ্চে ভাষণ দেননি; তিনি মানুষের পাশে বসেছেন, তাদের কথা শুনেছেন।
স্বাধীনতার পর আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম এক ন্যায়ভিত্তিক সমাজের—যেখানে উর্বর মাটি, কর্মশক্তি ও মানবিক মর্যাদা মিলেমিশে উন্নতির পথ দেখাবে। ‘সোনার বাংলা’ নামে পরিচিত এই দেশে প্রত্যেক শিশুর চোখে থাকবে আলো, প্রত্যেক হৃদয়ে থাকবে সম্ভাবনা।
জুলাই গণঅভ্যুত্থান কোনো একক ব্যক্তি বা দলের ছিল না; এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই আপামর জনগণের। অথচ সেই জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জুলাই সনদকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে এবং ‘হ্যাঁ’–‘না’ ভোটের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে।
বাণিজ্য ও সামাজিক সম্পর্কও ধীরে ধীরে শহরের কেন্দ্র ছেড়ে সরে গেছে। বড় শপিং মল, আউটলেট, নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক অঞ্চল—সবই সুবিধাজনক ও কার্যকর। কিন্তু সেখানে নেই অপ্রত্যাশিত দেখা হওয়ার আনন্দ, ধীরে বসে থাকার অবকাশ, বা হঠাৎ আলাপের উষ্ণতা।